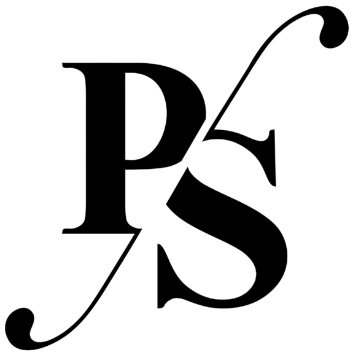‘কেন আরও ভালবেসে যেতে পারে না হৃদয়’
মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই আদ্যন্ত রোম্যান্টিক গানটির সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে কোনও শ্যামাসঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক নেই। তবু মানবেন্দ্র যখন গেয়ে ওঠেন, ‘আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি/ তবু মনে হয় এ যেন গো কিছু নয়/ কেন আরও ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়...’ তখন আমার মনে পড়ে যায় ১৮৮১ সালের উজ্জ্বল চোখের এক ১৮ বছর বয়সী কিশোরের কথা।
চরম অর্থকষ্টে ভুগছে সেই কিশোর। প্রৌঢ় পাগলাটে গুরু সেই কিশোরকে তাঁর ঘরের পাশেই মন্দিরটি আঙুল দেখিয়ে বললেন, ‘ওখানে যা, মা–র কাছে যা চাইবি, মা তোকে তাই দেবে।’
অনাহার–অর্থকষ্টে ক্লিষ্ট কিশোরটি যখন হেঁটে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের দালানে হাঁটু গেড়ে বসল হাতজোড় করে, কিছুতেই তাঁর মুখ থেকে টাকার কথা বেরলো না। বদলে সে চেয়ে বসল, আরও আরও ভক্তি। চেয়ে বসল আরও বেশি করে ভালবাসার ক্ষমতা।
একবার নয়, তিনবার ঘটেছিল এই ঘটনা। একবারও নিজের জন্য টাকাপয়সা চাইতে পারেনি সেদিনের নরেন্দ্রনাথ দত্ত।
দেখবেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেভাবে প্রেমপর্যায় আর পূজাপর্যায়ের গান মিলেমিশে এক হয়ে যায়। আলাদা করে বোঝাই যায় না কোনটা প্রেমের গান, কোনটা ভক্তির গান। প্রেম হোক বা ভক্তি— শ্যামাসঙ্গীতেও সেই একই জিনিস ঘটে। ফলাফল যাই হোক, আরও বেশি করে ভালবাসতে চাওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না।
এর ওপরে বাঙালি হওয়ার একটা সুবিধা আছে। এদেশের আর পাঁচটা জাতির মতো নই আমরা। ভক্তি বা ভালবাসাই আমাদের ঈশ্বরসাধনার একমাত্র মার্গ নয়। ঈশ্বরী একাধারে আমাদের ঘরের মা। ঘরের মেয়ে। তাঁর কাছে অভিযোগ করা যায়, অভিমানে নালিশ করা যায়, তাঁকে বিদ্রুপ করা যায়। কার্যক্ষেত্রে রেগে গিয়ে গালাগালও করা যায়।
ঘুরেফিরে তো সেই একই ব্যাপার। রাগ তো আমরা তার ওপরেই করি, যার ওপরে আমাদের নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসা আছে। তার কাছ থেকে কিছু পাই বা না পাই, ভালবাসায় কোনও খামতি আসে না।
ভালবাসা বলতে আপনি কী বোঝেন? আমি ভালবাসা বলতে বুঝি, কোনও প্রত্যাশা ছাড়াই শুধু দিয়ে যাওয়া। তার প্রতিদান পাই বা না পাই, কিচ্ছু আসে যায় না। যদি আপনার প্রত্যাশা থাকে, জানবেন আপনি ভালবাসছেন না। এটা দেওয়ার বিনিময়ে ওটা পাব, এই ধরনের একটা ডিল করছেন। একমাত্র সন্তান ছাড়া এইভাবে কি আমরা আর কাউকে ভালবাসতে পারি? বোধহয় পারি না।
ঠিক সেই কারণেই শ্যামাসঙ্গীত শুনলে কারও কারও মাতৃভাব জাগে। আর আমার জাগে পিতৃত্ব।
আমি মন্ত্রতন্ত্র বুঝি না আমিও তন্ত্রমন্ত্র কিছুই বুঝি না। সত্যিই বুঝি না। কিন্তু আমি পিতার স্নেহ বুঝি। বুঝি কীভাবে যিনি একজনের চোখে মা, তিনিই কীভাবে আর একজনের চোখে কন্যা হয়ে যান।
আমি বুঝি রামপ্রসাদ সেন। বুঝি অপত্যস্নেহ। বুঝি পুত্রসন্তান রূপে হোক কিংবা পিতারূপে— একজন পুরুষের মা অথবা কন্যাকে পাওয়ার আকূতি। আর বুঝি কেন কন্যা হোক বা মাতা, আরাধ্যা জগদীশ্বরী তাঁর সাধকের থেকে দূরত্ব বাড়িয়েই চলেন, কেন কষ্ট দেন। কোন যন্ত্রণা থেকে রামপ্রসাদকে লিখতে হয়, ‘মায়ের এমনি বিচার বটে/ যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে/ তার কপালে বিপদ ঘটে’।
আমি বুঝি, এখন একটু একটু বুঝি।
ইতিহাস দেখুন। যাঁরা যাঁরা এ বাংলার মাটিতে ঈশ্বরীর সাধনা করেছেন, প্রত্যেকের জীবন ছিল অসীম দুঃখে ভরা। বলা হয়, কালীভক্ত যাঁরা হন, তাঁদের গোটা জীবন কাটে দুঃখে। রামপ্রসাদ থেকে কমলাকান্ত— বাংলা শ্যামাসঙ্গীতের বিপুল সম্ভার ঘেঁটে দেখুন, অভিযোগ থেকে গালাগাল— সবই পাবেন। খুব সিগনিফিক্যান্ট ব্যতিক্রম একটাই, সেই তথ্য এখানে ভাগ করে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। ‘দেবী’ ফিল্মে সত্যজিৎ রায় নিজে রামপ্রসাদী সুরে একটা শ্যামাসঙ্গীত লিখেছিলেন— ‘এবার তোকে চিনেছি মা’। খুব খটকা লেগেছিল সিনেমাটা নিয়ে পড়ার সময়। বাংলায় লাখেলাখে শ্যামাসঙ্গীত রয়েছে। কী দরকার পড়েছিল সত্যজিতের নিজে হাতে শ্যামাসঙ্গীত লেখার? ক্রমশ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বুঝলাম, শ্যামাসঙ্গীতে ‘আমাকে অমুক জিনিসটা বা অমুক সমৃদ্ধিটা দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ’— এই ধরনের ধন্যবাদজ্ঞাপক গান খুব বেশি নেই। সত্যজিতের দেবী মনে করুন। শুরুর দিকে দৃশ্যে জমিদারবাড়ির মন্দিরের সিঁড়িতে বসে বৃদ্ধ ভিখারী কোলে নাতিকে নিয়ে গাইছেন, ‘মা মা বলে আর ডাকব না/
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা’। সেই ভিখারীর নাতিরই যখন ‘দেবীকৃপায়’ রোগ সেরে যায়, তখন তাঁর মুখ দিয়ে গাওয়ানোর জন্য সত্যজিৎ গান লেখেন, ‘যে বলে তোরে পাষাণী, তারে আমি বেকুব মানি/ আমি মনে জানি, প্রাণে জানি/ পাষাণের ওই কী মহিমা’।
কিন্তু রামকৃষ্ণ কিংবা রামপ্রসাদ থেকে কমলাকান্ত, বাস্তবের কালীসাধকদের সঙ্গে এমনটা হয় না। হয়নি। গোটা জীবন অসীম কষ্টে কাটিয়েছেন তাঁরা। জগদীশ্বরী বোধহয় আজীবন দুঃখের গনগনে আগুনে ভক্তকে সেঁকে নিয়ে দেখে নিতে চান, তাঁর ওপর থেকে ভক্তের বিশ্বাস টলে কি না। প্রকৃত ভক্তের আস্থা অবশ্য টলে না। যে সদর্পে গেয়ে ওঠে,
‘ভূতলে আনিয়ে মা গো করলি আমায় লোহাপেটা
তবু কালী কালী বলে ডাকি, সাবাশ আমার বুকের পাটা।’ (রামপ্রসাদ সেন, ‘কালী সব ঘুচালি ল্যাঠা’ গানের অংশ)
শুনতে শুনতে মনে হয়, হৃদয়ের দপ্তর না পাল্টানোর এই কমিটমেন্ট রাখার জন্য কী বিপুল পরিমাণ ভালবাসারই না দরকার হয়! ঈশ্বরী সাধনার নানা ভাব আছে। মাতৃরূপ, ভার্যারূপের মতো কন্যারূপও একটা রূপ। রামপ্রসাদ কন্যারূপে কালীসাধনা করেছিলেন। এই কন্যারূপই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে। তার জন্য আমার আস্তিক হওয়ার দরকার পড়েনি। বাপ হওয়ার পরে বুঝেছি, সন্তানই আমাদের জীবনে একমাত্র মানুষ, যাকে আমরা ওই নিঃস্বার্থ এবং নিঃশর্ত ভালবাসতে পারি। একইসঙ্গে তাকে ‘কেন আরও ভালবেসে যেতে পারে না হৃদয়’ এ প্রশ্নও আমার মনে থেকেই গেছে।
আমি এমন এক পরিবারে জন্মেছি, যেখানে বিপত্তারিণী থেকে শুরু করে দুর্গাপুজো— সবই হয়। তবুও আমি নাস্তিক। কোনও প্রচলিত ধর্মাচারণ করি না। পৈতে নিইনি। ধারণও করি না। গত দশ বছরে দেশের রাজনীতিতে সংখ্যাগুরুদের আস্ফালন আমাকে আরও ধর্মবিমুখ করে দিয়েছে।
এই অবধি ঠিকঠাকই চলছিল।
তারপর ২০১৭ সালের ২৬ জুলাই কোনও এক ভোরবেলা একটা একদিন বয়সী গোলাপি রঙের তুলোর দলাকে যখন নিজে কোলে নিলাম এবং সামান্য সাধ্যসাধনাতেই দাঁতবিহীন ফোকলা মুখে সে আমার দিকে এক গাল হাসল, তখন মনে হল এ হাসি আমার চেনা। কিন্তু কোথায় এ হাসি আমি দেখেছি, তা মনে করতে পারতাম না কিছুতেই।
সেটা মনে পড়ল ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে। প্রোজেক্ট মায়ার হাত ধরে।
এই শ্যামাসঙ্গীতের ব্যান্ডটা আমার শুধু সাঙ্গীতিক বোধই নয়, চিন্তাভাবনাও পাল্টে দিলো। রাজর্ষিদার কণ্ঠকে আমি কোনও দিন লজিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারিনি। কোনও মায়াবলে এই লোকটা এই দরদে এই ভাবে গাইতে পারে, তা আমার যুক্তিবুদ্ধির অতীত। যাঁর গান রাজর্ষিদা গায়, গলায় স্বয়ং সেই ঈশ্বরীর বাস না থাকলে অমন গাওয়া যায় না। সেই প্রোজেক্ট মায়া শুনতে শুনতেই মনে পড়ে গেল এই সেম স্মিত হাসি আমি দেখেছি, আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে কালীপুজোর সময়। প্রতিমার দু’পাশের ধুনুচি থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠে পিছনটা ঝাপসা হয়ে গেছে, ক্যামেরার পোট্রের্ট মোডে ছবি তুললে যেমন হয়। প্রতিমার নীলচে মুখে আলগা একটা হাসি লেগেই আছে। কোনও স্নেহাস্পদের দিকে তাঁর পিতৃস্থানীয় কেউ তাকে প্রতিদানে যে হাসিটা ফিরিয়ে দেয় কেউ— সেরকম হাসি।
এর কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। আমি চিরকাল লজিকের দাস। এখানে লজিকও নেই। কিন্তু আমি মিল পাই। কী করব? আমি রিজিড নই। চিন্তার ফ্রি–ফ্লোতে বিশ্বাস করি। চিন্তাকে আটকাই না। ওটা মৌলবাদের লক্ষণ। তাই চিন্তাকে ভেসে যেতে দিচ্ছি। আমি বই পড়ছি। গান শুনছি। চেষ্টা করছি চিন্তাটাকে কানেক্ট করার। আমি কি আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস রাখতে শুরু করেছি? আমার নিজের কাছেও উত্তর নেই। আপাতত একটা জার্নি শুরু হয়েছে। হয়তো জার্নির শেষে গিয়ে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব।
আমি জানি, ঈশ্বর হলেন অঙ্কের এক্স। ছোটবেলায় অঙ্ক কষার সময় অজ্ঞাত মানের ভ্যালু এক্স ধরে নিলে অঙ্ক করতে সুবিধা হতো। অঙ্ক শেষ হলে এক্সের আর কোনও অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু ততক্ষণে যে ভ্যালুটা আমি খুঁজছিলাম মাথা ঘামিয়ে, সেটা আমার খাতার পাতায় বের করা হয়ে গেছে। তাই এক্সের অস্তিত্ব আছে মনে করলে আছে, নেই মনে করলে নেই। ঈশ্বরেরও তাই। আমার মেয়েকে নতুনভাবে চেনার জন্য, নতুনভাবে ভালবাসার জন্য এক্স।
আমি সেই দেশে, সেই বাংলায় জন্মেছি, যেখানে মা–কে কন্যার মতো তুই সম্বোধনে ডাকা হয়, আর কন্যাকে ডাকা হয় মা বলে। ঈশ্বরী সম্পর্কে আমার ঠাকুমা বলতেন, মা ভাবলে মা, মেয়ে ভাবলে মেয়ে। আমি জানি না তিনি সত্যিই আছেন কি না। আমি জানি আমার একজন মা আছেন। আমি জানি আমার একটি কন্যা আছে। সে একদিন বড় হবে। সেও একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, ঈশ্বরী বলে কেউ আছেন কি না। থাকলে আমি তাঁকে দেখেছি কি না।
শুরুতে নরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা বলছিলাম। তখনও তিনি বিবেকানন্দ হননি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান ছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?’
রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, ‘হ্যাঁ। এই তোকে দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্ট করে।’
ঠিক এই উত্তরই আমিও ঘণ্টেকে দেবো। কারণ, ওকে কোলে নেওয়ার সেই প্রথম দিনে যখন আমি ওর হাসি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে আমি হুবহু আমার সেই ধুনুচির ধোঁয়ায় কৃষ্ণনগরের বাড়ির পুজোয় প্রতিমার স্মিত মুখের অবিকল মিল পেয়েছি।
আজ একটু পরেই রাস্তাঘাট থেকে ঘরের কোণ— সবই আলোয় আলোয় সেজে উঠবে। দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে ঘর আলো করে আজ আমার সেই মা আমারই কন্যার সাজে সেজে পুজো নিতে ছেলের ঘরে ফিরবে। আলোয় আলোয় দেখতে পাব, আমার মেয়ের এলোকেশী লোলজ্বিহা ভীষণ রূপ বদলে যাচ্ছে গালফোলা ঠোঁট উল্টে অভিমানী চোখে পিতার তাকানো শিশুকন্যার রূপে। তাকে কোলে নিতেই সে আমার বুকে মাথা এলিয়ে দেবে। একহাতের বুড়ো আঙুল মুখে পুরে চুষতে চুষতে আর একহাত বুলিয়ে দেবে আমার মাথায়, ঠিক যেমন আমার পাশে শুয়ে ঘুমনোর সময় মিঠাই করে। তার হাতের স্পর্শে এক না একদিন আমার সব কষ্ট, সব সন্তাপ সব অপেক্ষার যন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে। যতদূরে থাকুক, সে আসবেই। কারণ স্বয়ং রামপ্রসাদ বলে গেছেন, ‘যদি ডাকার মতো ডাকতে তোকে পারি, তুই আসবিনে তোর এমন সাধ্য নেই।’
আমার কাছে না এসে সে যাবেটা কোথায়?
আপানারা যাকে মা বলেন, আমি যার মুখের মধ্যে আমার কন্যার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই— আমার সেই মেয়ের হাতের স্পর্শে যেন এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কল্যাণ হয়।’
অপূর্ব এই ছবিটি কে তুলেছেন, জানি না। জানলে ক্রেডিট দেবো