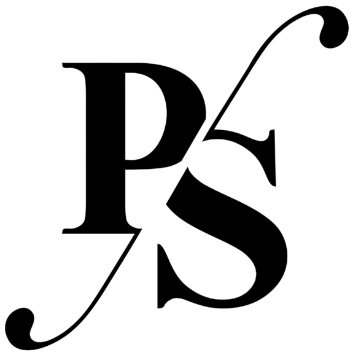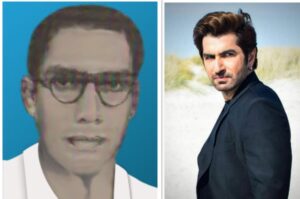মনমোহন মিত্র এসেছেন। আগন্তুকের মনমোহন মিত্র। যিনি আমাদের আত্মীয় হতেও পারেন, নাও পারেন। যেহেতু তিনি যে সত্যিই আমাদের আত্মীয়, তা মেনে নিতে আমাদের সংকোচ আছে, সংশয় আছে, ফলত তাঁর যে গুরুত্ব পাওয়ার কথা, তা তাঁকে আমরা দিচ্ছি না। সমকাল দিচ্ছে না।
আমি রূপম ইসলামের কথা বলছি। বলছি রূপম এককের কথা। তাঁকেই আগন্তুক ফিল্মের মনমোহন মিত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ পয়লা বৈশাখের এককের পর থেকে আমি রূপমের সঙ্গে মনমোহন মিত্রের যে মিলগুলো পাচ্ছি, তাকে ইংরেজিতে বলে ‘আনক্যানি সিমিলারিটিজ’। গা ছমছমে সাদৃশ্য!
রূপম গাইছিলেন। রূপম বলছিলেন। মাত্র ১৪দিনের ব্যবধানে ফের একটা একক। আগেরটি ৩ ঘণ্টার সামান্য বেশি সময়ের। গতকালেরটি চারঘণ্টা দশ মিনিটের সামান্য বেশি। একা হাতে গিটার এবং কি-বোর্ড। গলায় হারমোনিকা। অনায়াসে ব্যবহার করছেন ছ’টি প্যাডেল! কোনও কোনও প্যাডেলে একাধিক সুইচ। যে কোনও পেশাদার যন্ত্রশিল্পীই জানবেন, কাজটা কতটা কঠিন। একটা মানুষ কোনও লিরিক স্ট্যান্ড ছাড়া, কোনও লিখিত সং লিস্ট ছাড়া, গাইছেন, কথা বলছেন, এটা চোখের সামনে দেখাটাও কেমন যেন সুপারহিরোর ফিল্মের মতো লাগে। তাও আবার কী গাইছেন? না, যে গানগুলো তিনি কালেভদ্রে গেয়ে থাকেন। যা তার নিয়মিত চর্চার মধ্যে পড়ে না!
শ্রোতারা শুনছেন। বুঁদ হচ্ছেন। রূপম যেন তাঁদের নড়া ধরিয়ে বসিয়ে রেখেছেন সম্মোহিতের মতো। হিসেব করে দেখলাম, দুটো এককের সং লিস্টের মধ্যে মাত্র দু’টি গান ‘কমন’।’যাব হারিয়ে’, ‘অতিবেগুনি চালাকি’ এবং ‘আমি যাই’। চমকপ্রদ না?
রূপম বলছিলেন তাঁর জীবনের গল্প। আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে তাঁর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার গল্প। কেরিয়ারের শুরুতে কীভাবে দিনের পর দিন, টেলিভিশন চ্যানেল, প্রথমসারির ম্যাগাজিনের সাংবাদিকরা তাঁকে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। রূপমের অপরাধ? তিনি বাংলা রক সঙ্গীত করতেন, করেন।
সময়টা মনে করুন, ন’য়ের দশকের শেষের দিক। বাংলা ব্যান্ড, বাংলা রক প্রতিষ্ঠা হওয়া তখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। চাঁদ–ফুল–পাখি নিয়ে এতদিন যে বাংলা গান (যা কি না ‘মধুর’ হওয়ার সংজ্ঞা নিরূপণ করে) গ্যাদগ্যাদে মিষ্টত্ব ছড়িয়ে এসেছে, সেই অচলায়তনে (নাকি অটলায়তন?) প্রথম ঘা মেরেছেন সুমন। তাতে প্রথাগত বাংলাগানে মৌরসী পাট্টার দেওয়ালে ফাটল ধরেছে ঠিকই, তবে দেওয়াল তখনও হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েনি।
রূপমের আবির্ভাব ঠিক সেই সময়ে। তিনি আসবেন, কাঁচা আবেগের পদাঘাতে দেওয়াল ভাঙবেন ফসিল্স ওয়ান দিয়ে। এবং তা রুখে দেওয়ার চেষ্টা করবেন কিছু পক্ককেশ বৃদ্ধ! সংস্কৃতির ধারকবাহকরা।
পৃথিবীর রক সঙ্গীতের ইতিহাস যদি দেখেন, দেখবেন, কোনও দিনই রক মিউজিকের যাত্রাপথ খুব একটা ফুলেল ছিল না। যুগেযুগে রকস্টাররা ‘বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে’ পথের কাঁটা রক্তমাখা চরণতলে একলা দলেই এগিয়ে গিয়েছেন। রক মিউজিক কোনওদিনই ‘ভদ্দরনোক’–দের গান নয়। ভাগ্যিস নয়। হলে আজও আমরা ঘাড়ে পাউডার মেখে হারমোনিয়ামের সামনে বসে গলা অকারণ মোটা ও গম্ভীর করে ওই চাঁদ–ফুল–পাতার গানই গেয়ে যেতাম। একটা ‘অ্যাসিড’ কিংবা একটা ‘ক্ষুধার্ত মাংসাশী’ আসত না।
রূপমের প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হওয়ার গল্প শুনতে শুনতে মনে পড়ে যাচ্ছিল আগন্তুকের পৃথ্বীশ সেনগুপ্তের কথা। তথাকথিক সভ্য ও ভদ্রসমাজের প্রতিনিধি হয়ে যিনি বারবার অপদস্থ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন আগন্তুক মনমোহনকে। জবাবে বারবার মনমোহন পাল্টা প্রশ্ন তুলছিলেন, সভ্য কারা? সভ্যতার ভবিষ্যৎ কারা ঠিক করবে? একই প্রশ্ন রূপমেরও।
কারা ঠিক করবে বাংলা গানের সভ্যতার ভবিষ্যৎ? কারা ঠিক করবে, এটা গান হচ্ছে কি হচ্ছে না?
মনমোহন মনে করতেন, পৃথিবী একটাই দেশ। প্রতিটি মানুষ আমার সহোদর। ঠিক যেমনটা মনে করতেন লালন কিংবা লেনন। ঠিক তেমনই মনে করেন রূপমও। স্মৃতিরোমন্থনে জানালেন, স্রেফ ধর্মীয় কারণে কীভাবে তাঁর মিউজিশিয়ান পিতা ও মাতাকে বেছে বেছে ইসলামী গান বানানোর বরাতই দিত রেডিও সংস্থা। অথচ শ’য়ে শ’য়ে দেশাত্মবোধক গান ও গণসঙ্গীতও ছিল তাঁদের ঝুলিতে।
পরবর্তীতে এই টেলিভিশন সংস্থা রূপমকে পেয়েছিল। যাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে ‘ইসলাম’। তাঁরও ভবিতব্য হল ইদের গান বানানোর বরাত পাওয়া। ‘প্রথাগত ধর্মবিহীন’ রূপম তাঁর পিতা কিংবা মাতার মতো সয়ে নেওয়ার বান্দা নন। খুশির ইদের আগে তিনি লিখলেন ‘কী লাভ’–এর মতো গান। যে গান ভেদাভেদের বিরুদ্ধে কথা বলে। যে গান বলে, পৃথিবীর একজন মানুষও যাতে অসুখী না থাকেন। যদি থাকেন, তাহলে উৎসব পালনের নৈতিক অধিকার আমাদের নেই।
কর্তাদের অগোচরে গেয়েও ফেললেন, সেই গান সম্প্রচারিতও হয়ে গেল। তাঁরা যে বিশেষ প্রীত হননি, তা বলাই বাহুল্য।
ঠিক যেমন প্রীত হননি ‘আগন্তুক’–এ পৃথ্বীশ সেনগুপ্ত। মনে পড়ে যায় বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের সেরা সিকোয়েন্সগুলোর একটা...
—‘আপনি ধর্ম মানেন মিস্টার মিত্র?’
—‘যে জিনিস মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে, তা আমি মানি না। অর্গানাইজড রিলিজিয়ন তো সেটা করেই।’
ভেদাভেদ!
আবারও আলাদা করে লিখতে হল এই শব্দটা। ভেদাভেদ শুধু ধর্মীয়? শৈল্পিক নয়? নামের শেষে ইসলাম থাকার সুবাদে একজন বহুমুখী শিল্পীকে বারংবার ইসলামি গান লিখতে গাইতে বাধ্য করা। এটা ভেদাভেদ নয়?
এই ভেদাভেদ মেটানোর জন্যই দরকার পড়ে রূপমের মতো একজন আদ্যন্ত ‘ঢ্যামনা’ লোকের। যিনি টেলিভিশম কর্তাদের ফরমানে খুশির ইদ উপলক্ষে লিখে ও গেয়ে ফেলতে পারেন ‘কী লাভ’–এর মতো একটা গান।
যে গান বলছে...
‘একফালি এই চাঁদের আলোয়
ফের স্বপ্ন দেখা কি সম্ভব?
মনে পড়ে কি সেই ক্লিশে শব্দটা
বিপ্লব...’
অথবা
‘যদি খুশির ফানুস হাওয়ায় ভাসিয়ে
দেয় হুঁশ
তবে বলো
তুমি কেমন মানুষ’
কিংবা
‘আমি খুশি হতে রাজি যদি কমে যায় খুশিদের দাম
্আজ সব বোঝাপড়া হোক চাঁদকে দায়িত্ব দিলাম
চলো কমরেড ভেঙে দিই
গোটা পৃথিবীর উপবাস’
এই রে! কমরেড শব্দটা কোট করে ফেললাম! একসময় এক বামদলের তরুণ সমর্থকরা (বামপন্থী বন্ধুবর সৌম্যশান্ত রিজওয়ান রক্ষিত ভাল জানবেন) একসময় তাঁকে ছিঁড়ে খেয়েছিল, কেন তিনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের জিঙ্গলে গলা মিলিয়েছেন বলে। পরবর্তীতে রূপমেরই গানের লাইন ‘শাসন শুধু শাসন নয়, আসল অস্ত্র সমন্বয়’ বামপন্থীদের সেই দলেরই নির্বাচনী প্রচারে দেওয়াল লিখনে জ্বলজ্বল করেছে।
রূপম এরকমই। এই তিলেখচ্চর লোকটাকে না যায় হজম করা, না যায় প্রত্যাখ্যান করা। দিনের শেষে তাঁর কাছেই ফিরতে হয়। যেমন রূপমের কাছেই ফিরতে হয়েছিল কেরিয়ারের শুরুতে রূপমকে প্রত্যাখ্যান করা টিভি চ্যানেলকে, রূপমকে অপমান করা ম্যাগাজিনকে।
যেমন ফিরতে হয়েছিল আগন্তুক মনমোহনকে অপমান করে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা তাঁদের ভাগ্নী ও ভাগ্নীর পরিবারকে। রূপম যখন গল্পেগল্পে বলেন তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া রেকর্ড কোম্পানির মালিকের ফের কাজের প্রস্তাব দেওয়ার কাহিনী, আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগন্তুকের সেই দৃশ্য। সাঁওতালদের গ্রামে খড়ের গাদায় হেলান দিয়ে বসে আছেন মনমোহন। ভাগ্নী অনিলা ও তাঁর পরিবার এসেছে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মনমোহন নির্বিকার, নিরুত্তাপ। মেধাবী ছাত্র মনমোহন চাইলে কুনোব্যাঙের সচ্ছলতায় আর পাঁচটা গড়পড়তা বাঙালির মতো বাঙালির মতো সুখের জীবন বেছে নিতে পারতেন। অর্থ, স্থিতি, নিরাপত্তা সব থাকত জীবনে। তা না করে তিনি ছুটে চললে অদেখাকে দেখার নেশায়। রূপমও তেমনই, বহু সংগ্রামের পরে যখন ফসিলসের হাত ধরে কেরিয়ারে স্থিতি পেলেন, খ্যাতির শিখরে উঠলেন ফসিলসেই মনোনিবেশ করে থাকতে পারতেন।
তার পাশাপাশি তিনি কী করলেন? না, ব্র্যান্ড একক তৈরি করলেন। যেখানে গাওয়া হয়, তাঁর ‘অখ্যাত’, ‘অশ্রুত’, ‘আনরিলিজড’ গানগুলো। তাও নাকি শ্রোতাদের মুখেমুখে মুখস্থ। ঠিক যেভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ত অতীতের লোকগান! ঠিক সেইভাবেই। যে গান লিখে তিনি জাতীয় পুরস্কার পেলেন, অন্য কেউ হলে তা প্রতিটি শো–তে গাইতেন। রূপম সেখানে কী করেন, না অনাদরের সন্তানের মতো কালেভদ্রে গেয়ে থাকেন ‘এই তো আমি’। এই নির্লিপ্ত মনোভাব, উদাসীনতা, ত্যাগের অভ্যাস তিনি কী করে অর্জন করলেন কে জানে! এসব দেখেশুনে আগন্তুকের সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মনমোহনের সাঁওতালদের গ্রামে খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে বসে থাকার দৃশ্য মাথায় আসবে না?
মনমোহনের সঙ্গে রূপমের সাদৃশ্য পেয়েই চোখে ভেসে ওঠে আরও এক দৃশ্য। ময়দানে ভাগ্নীর পুত্র সাত্যকির ও তার বন্ধুদের সঙ্গে বসে ব্যাখ্যা করছেন সূর্যগ্রহণের মহাজাগতিক রহস্য। বলে চলেছেন দেশবিদেশের গল্প। খুলে দিচ্ছেন একের পর মনের দরজা। ঠিক সেভাবেই পয়লা এককে ডব্লিসিজেডের এককে রূপমকে ঘিরে বসে ত্রিশজন বন্ধু, যাঁরা ওই সাত্যকির মতোই শুনে চলেছেন দানিকেন, গ্রহান্তরের জীব অথবা স্টিফেন হকিংয়ের গল্প। গল্প আফ্রিকার আদিবাসীদের, গল্প মানবসভ্যতার ইতিহাসের, গল্প এ বিশ্ব সৃষ্টির!
আসরের শেষে রূপম অবশ্য বললেন না। তবে না বললেও মগজে গমগম করতে থাকল সাত্যকিকে দেওয়া মনমোহনের সেই শিক্ষা— ‘আমরা কূপমণ্ডুক হব না।’
আপনার গানে সুর আছে, মাধুর্য নেই! তরুণ রূপমকে বলেছিলেন কোনও এক দূরদর্শনের আধিকারিক। তার কয়েকবছর পরে অবশ্য তাঁরাই ফের গাইতে ডাকবেন রূপমকে। ততদিনে রূপম যে উচ্চতায় উঠে গেছেন, তাঁকে ‘অ্যাফোর্ড’ করার ক্ষমতা আর তাঁদের নেই। ওই চ্যানেলের অধিকর্তাকে কি ‘বিদায়’ গানটি শুনিয়েছিলেন রূপম? মাধুর্য বলতে যদি শুধু কেউ কালোয়াতি গানের গিটকিরি বুঝে থাকেন তাহলে অন্য কথা। নইলে যে বুকফাটা আর্তনাদ, যে নিখাদ বিষাদ এবং যে প্রবল একাকিত্বের কথা এই গান বলে, তার মাধুর্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারতেন ওই অধিকর্তা।
রূপম স্বীকার করবেন না, মানতেও চাইবেন না হয়তো— শুধু সেই সময়ের টেলিভিশন চ্যানেল, রেডিও অথবা সাংবাদিকদের একাংশের ভুল নয়, বাংলায় ভিন্নধারার গানের দিকপালরাও বোধহয় এই অপমানের দায় এড়াতে পারেন না। যে সুমন নতুন ধারার বাংলা গান আনলেন, ফোনে ও ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় রূপমের গান শুনে বাহবাও দিলেন, তিনি তাঁর একটিও বইতে রূপমের কথা একটি লাইনও লিখলেন না। সুমনের নাম নিয়ে রূপম একটি বিরূপ মন্তব্যও করবেন না, কারণ তিনি ওঁকে আজও গুরু বলে মানেন। আজও সুমনের প্রসঙ্গ উঠলে রূপমের চোখেমুখে জ্যোতি খেলা করে যায়। তবুও গায়ক সুমনের গুণমুগ্ধ হয়েও বলছি, আমার এই সুশীলতার দায় নেই। আমার মনে তো এই প্রশ্নও উঠছে, কেন সুমনের একটিও গানসংক্রান্ত বইতে ফসিলস কিংবা রূপম সম্পর্কে একটিও লাইন নেই। সুমনের বই বাংলা গানে একটি প্রামাণ্য দলিল হতে পারতো। রূপমের গানের প্রশংসা করেও কেন তাঁর বইতে একটিও শব্দ না লেখার দ্বিচারিতাটা সুমনরা করতে পারেন? এটাও কি ওই টিভি চ্যানেলের আধিকারিকের না শুনেই রূপমের ডেমো প্রত্যাখ্যান করা, রূপমকে রেডিও কর্তাদের ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামি গান বেছে বেছে দেওয়া অথবা জনপ্রিয় ম্যাগাজিনের সাংবাদিকের ভিত্তিহীন অভিযোগ করার মতোই অপরাধ নয়?
রূপম প্রকৃতিগতভাবে শিক্ষক। এ সবের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি ক্লাস নিয়ে যান। কালও নিলেন। দিলেন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার পাঠ। বোঝালেন, স্তব্ধ জীবনের অপকারিতা। বোঝালেন, কাউকে অন্তত সব ক্রুশ কাঁধে নিতে হয়, যন্ত্রণায় দায়ভার সহ্য করতে হয়। তবেই না ‘বিদায়’ লেখা যায়!
অনুষ্ঠানের শেষে চোখাচোখি হতে হাল্কা হাসলেন রূপম। যেন করতে চাইলেন সেই প্রশ্নটাই, যা বিদায় নেওয়ার সময় মনমোহন করেছিলেন সাত্যকিকে,
—‘আমরা কী হব না?’
যাতে কেউ শুনতে না পায়, মনেমনেই আমিও ফিসফিস করে একগাল হেসে উত্তর দিয়ে ফেললাম
—‘কূপমণ্ডুক!’
ছবি: Antaroop Chakraborty